
২০১০সাল থেকেই ঢাকা থিয়েটারের সাথে জড়িত। ছোট খাটো ডায়লগ লেখা, নাটক গুছিয়ে লেখা এসব করতেই করতে বই নিয়েই সময় কাটতো ঢেরবেশি। বন্ধু বান্ধবের সাথে আড্ডা আর শখের ছবি আঁকার পাশাপাশি কিছু কিছু লেখা যেনো আসতে শুরু করলো ভেতর থেকে। কতশত কবিতা লিখিয়ে নিলো প্রেমিকেরা, কিছু লিখতাম প্রেমের শুরুতে আর কিছু লিখতাম প্রেমের শেষে। ওই যাকে বলে বিরহে। আমার ভেতর এই দুইধারি তালোয়ারের খোঁজ আমিও তখন পাইনি সত্যি। কিন্তু বইয়ের ভেতর, খাতার মাঝে, ব্যাগে একটা ডায়েরি থাকবেই থাকবে আমার তা যেনো ছিলো বাধ্যতামূলক। যেখানেই যা দেখতাম তা নিয়ে যেনো কিছু লিখে ফেলা, কিছু বলতে চাওয়া। কিন্তু আমাদের সমাজে মুখে কুলুপ এঁটে থাকায় যেখানে রীতি সেখানে লিখবো কী আমি আর ভারি!
ইউনিভার্সিটির শেষের দিকের কথা হবে। হাস্যরসিক এক বান্ধবী ছিল আমার, নাম জেরিন। সেই সময় তাদের বাসায় যাওয়া, উঠাবসা খুব হতো। ভালো পরিবার ছিলো তাদের। বলতে গেলে বনেদী ব্যাপারটা আমি প্রথম ওই বাসাতেই দেখি। যেমন রূপোর বাটিতে খাবার দেয়া, কাঁসার গ্লাসে পানি দেয়া। সংসারের চারদিক ঝলমল করছে কাঁসার সোনালি রঙে আর রুপোর ছিটকে আসা উজ্জ্বলতায়। ওসব দেখে আমরা অভ্যস্ত নই বলেই আমাদের আগ্রহ একটু বেশিই ছিল বৈকি জেরিনকে নিয়ে।
ক্লাস সেরে বা ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে আমাদের আড্ডাটা হতো সিদ্ধেশ্বরী পি.বি.এস-এর ভেতর অথবা বাইরে। কয়েকমাস ধরেই খেয়াল করলাম জেরিন আর সেই আড্ডায় আসে না। নতুন প্রেম হয়েছে দেখে সবাই হাসাহাসি আর রসিকতা করেই অগ্রাহ্য করলাম আপাতত। সেমিস্টার ফাইনাল চলে আসলো, জেরিনের পাত্তা নাই। অনেকেরই পড়তে পড়তে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। বিয়ের দাওয়াতও খাচ্ছি দলবল মিলে। কেউ বিয়ের পর পড়া চালাচ্ছে, কেউ আর পড়ছে না। এসব সহনীয় পর্যায়ে চলে গিয়েছিলো ততদিনে। কিন্তু জেরিনের মতো কেউ লাপাত্তা হয়ে যায়নি। ফোন দিয়েও পাওয়া যাচ্ছে না। আমার বাড়তি আগ্রহ দেখে সবাই বলতে লাগলো জেরিন তোরে ছ্যাকা দিয়া চইলা গেছে। এখন ছ্যাকা হোক আর বোকা হোক, ভেতরটা জায়ফলের মতো খটমট করতে লাগলো। ততদিনে এটুকু বুঝতাম জয়ত্রী আর জায়ফল হলো সুখ আর দুঃখের মতো একই গাছের দুই ফল। জয়ত্রী হলো ওপরের অংশটুকু যা সুখ আর ভেতরে খুটখুট করতে থাকা দুঃখের বীজটি হলো জায়ফল।
যাইহোক সেমিস্টার ফাইনালের শেষের দিকে চলে গিয়েছিলাম। তার মাঝেই নিজেরও বিয়ের কথা চলছে। সব নিয়ে জেরিন যেনো ভাবনা থেকে অনুপস্থিত। বিয়ের দিন যেদিন হলুদ মাখানো হবে আর কিছুক্ষণ পর, আমার খুব করে মনে হলো জেরিনের কথা। কী জানি কী? আগপাছ কিছু না ভেবেই ছুটলাম শান্তিনগর জেরিনের বাড়ি। যেয়ে জানতে পারলাম এক ভয়ংকর সত্য। প্রেম করেছিলো জেরিন হিন্দু বংশের এক ছেলের সাথে। বাবা বাড়ি থেকে বের করে দেয়াতে পালিয়ে বিয়ে করেছিলো দুইজন।কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। এক বাসা ভাড়া করে সেই ছেলে তাকে ফেলে রেখেছিলো দিনের পর দিন। সামাজিক স্বীকৃতি দেয়া তো দুরস্ত, জড়িয়েছিল অন্য এক প্রেমে। আত্মহত্যার পথ সহজ মনে হয়েছিলো আমাদের সেই হাসিখুশি ছটফটে জেরিনের।
ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরে গেলাম, কেন জানি জেরিনের মায়ের কান্নাও খুব অসহ্য লাগছিলো। বেশিক্ষণ না থেকেই হেঁটে হেঁটে বাড়ি আসলাম। ভেতরে তোলপাড় আর মরা মাছের চোখ নিয়েই বসলাম বিয়ের পিঁড়িতে। অনেকেই আমার সেই উদাসীনতা দেখে ভেবেছিলো বিয়েতে বুঝি কনের সম্মতি নেই। কথায় আছে না ডেরা সাপে না কাটলেও অভিশাপে কাটে শত। আমার দশা তেমন। ডেরা সাপ মানে প্রেমে ছ্যাকা খাইনি তো কী হয়েছে? মানুষের মুখে মুখে রটে গেলো আমার বুঝি আগে প্রেম ছিলো।ভাগ্যিস বর বুঝদার ছিলো। তাই বিয়েটা খোঁটা ছাড়াই সম্পন্ন হলো। কিন্তু হলে কী হবে, ওই যে জায়ফল খুটখুট করছে মনের ভেতর তার কী হবে?
লিখতে বসলাম আমার জীবনের প্রথম উপন্যাস। ‘কাঁটাতারের পরিযান’। জেরিনকে মাথায় রেখে লিখলেও পালটে দিলাম নাম, ধর্ম। প্রধান চরিত্রের নাম রাখলাম সেঁজুতি। সেঁজুতিকে যথারীতি বাবা ত্যাজ্য করে ঘর থেকে বের করে দেয় মুসলমান তনয়-এর সাথে প্রেম করার পাপে। তনয়ের নামে ছাদনা তলায় সিঁথিতে সিঁদুর পরে সেঁজুতি ঠিকই কিন্তু শেষ পরিনতি হিসেবে সংসার করা হয়ে ওঠে না দুজনের। তবে জেরিনের যে অপমৃত্যু তার প্রতিবাদে আমার গল্পের নায়িকার আত্মহত্যা আমি লিখিনি।
আমি লিখেছি সেঁজুতির ঘুরে দাঁড়ানোর কথা যা চাইলে মেধাবী জেরিনও করতে পারতো। আমি লিখেছি সেঁজুতির মায়ের চরিত্রে আরেকজন শক্তিশালী নারী আন্না বসুর কথা যে বাবা আর মেয়ের মাঝে সেতু হয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করেছে চৌকস বুদ্ধিমত্তা দিয়ে।সেঁজুতির মনোবল আর আন্না বসুর বুদ্ধিমত্তা ও উদারতা সমাজে লিখে রাখতে চেয়েছি দৃষ্টান্ত হিসেবে। যদি কোন ঘরের মা, সন্তানের বিপদে দশভুজা দুর্গার মতো সব বিপদকে মোকাবিলা করে আর সমাজের মুখে চপেটাঘাত মারতে পারে তাহলে সমাজে কোন সন্তান আর মৃত্যু সহজ মনে করবে না বেঁচে থাকার চেয়ে।
সেঁজুতি আর আন্না বসু তাই শুধু আমার উপন্যাসের চরিত্রই না বরং তারা সব প্রশ্নের জবাব যা যুগ যুগ ধরে নারীদেরকে দুর্বল করে রেখেছে কখনো প্রেমের নামে, কখনও শরীরের নামে, আবার কখনও সমাজ সংসারের রাস্তায় রাস্তায়। হেরে যাওয়া মানুষের উঠে দাঁড়ানোর গল্প, সমাজকে নতুন করে সাজানোর দুই অনন্যসাধারণ চরিত্র সেঁজুতি আর আন্না বসু লিখে নিজের কাছেই মনে হয়েছে– এ যেনো আমি লিখিনি, কোন এক অদৃশ্য যেনো আমাকে দিয়ে লিখিয়েই নিয়েছে।
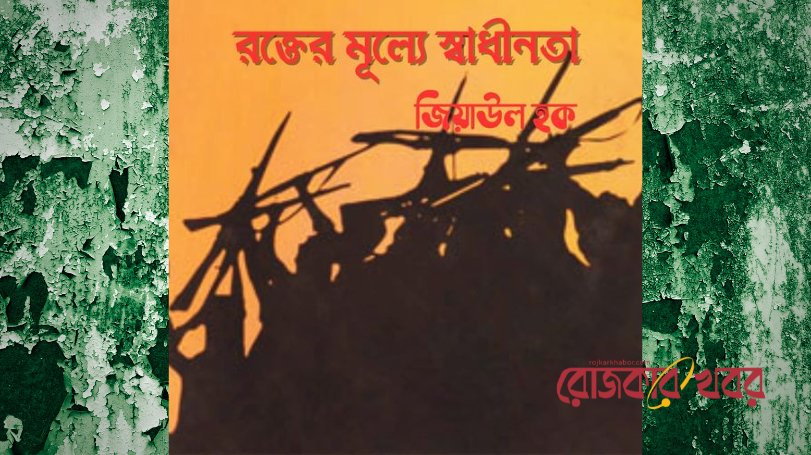
২.
মাজহারুল হক মন্টু। যশোরের ছাত্র রাজনীতির অঙ্গনে একটা পরিচিত নাম। স্নাতক শেষবর্ষের ছাত্র। স্কুলজীবন থেকেই ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত। ১৯৬৯ সালের স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকার বিরোধী গণঅভ্যুত্থানে তার রয়েছে অনন্য সাধারণ ভূমিকা। তাছাড়াও ১৯৭০ সালের পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পক্ষে সক্রিয় প্রচারণায় অংশগ্রহণ করে দলের ভেতরে নিজের অবস্থানকে পাকাপোক্ত করে তুলেছেন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়লাভের পর ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে আওয়ামী লীগের নানা টানাপোড়েন শুরু হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ১ মার্চ পূর্বে আহুত জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার পর সারা বাংলাদেশের মতো যশোর শহরেও প্রবল গণআন্দোলন শুরু হয়। তারই ধারাবাহিকতায় যশোর শহরের সর্বস্তরের ছাত্র-জনতা রাস্তায় নেমে এসে আন্দোলন শুরু করে। ৩ মার্চ ছাত্র-জনতার একটা মিছিল যশোর কালেক্টর ভবনে উড্ডীন পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা নামিয়ে একটা কালো পতাকা উত্তোলন করে যখন ফিরে আসছিল, তখন টিএন্ডটি ভবন থেকে পাকিস্তানি সেনারা গুলি বর্ষণ করলে চারুবালা নামে একজন গৃহবধূ নিহত হন। যার ফলে আন্দোলন আরও বেগবান হয়ে ওঠে। ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে থেকে বঙ্গবন্ধুর ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ ঘোষণা দেওয়ার পর থেকে সারা বাংলাদেশের মতো যশোরেও মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। তখন প্রতিদিনই শহরে চলতে থাকে প্রতিবাদ মিছিল, মিটিং।
২৩ মার্চ পাকিস্তানের জাতীয় দিবসে ছাত্রনেতা খান টিপু সুলতানের নেতৃত্বে যশোর শহরের নিয়াজ পার্কে প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ২৫ মার্চের রাতের আঁধারে হানাদার খান সেনারা যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে শহরে প্রবেশ করে রাস্তায় অবস্থানরত জনতার উপর নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করে অনেক সাধারণ মানুষকে হত্যা করে। অন্যদিকে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার পর থেকেই সারাদেশে প্রতিরোধযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। মাযহারুল হক মন্টু একজন ছাত্রনেতা হিসাবে যশোর শহরের আন্দোলনের প্রতিটা স্তরে যথাযথ ভূমিকা রাখার পাশাপশি শত্রুসেনাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু সাধারণ ৩০৩ রাইফেল নিয়ে যুদ্ধ করে আধৃুুনিক অস্ত্র সজ্জিত শত্রুসেনাদের সামনে টিকতে না পেরে পিছু হটে ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের উন্নত প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক অস্ত্র সজ্জিত হয়ে তার নেতৃত্বে একটা গেরিলা দল নিয়ে গত ৭ দিন আগে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে যশোর সদর থানার প্রত্যন্ত এলাকা কাশিমপুর গ্রামে সেল্টার গ্রহণ করেন। তিনি কলেজ পড়ুয়া একজন যুবক হলেও তাকে দেখে মনে হয় যেন একজন আর্মি অফিসার। কথাবার্তায় চালচলনে যেন আভিজাত্য ঝরে পড়ে। সামরিক বাহিনীতে সৈনিকদের যেমন কড়া আইন কানুনের মধ্যে থাকতে হয়, তেমনি তার অধীনের গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের থাকতে হয় কঠোর আইন কানুনের মধ্যে। পান থেকে চুন খসলেই কারো রেহাই নেই। সেন্টি ডিউটি বা রেকি করা কোন কাজেই সামান্যতম অবহেলাও তার সহ্য হয় না।
সেই কড়া স্বভাবের মাজহারুল হক মন্টুকে আজ কিন্তু খুব প্রাণখোলা এবং খোশমেজাজে দেখা যাচ্ছে। এর পেছনে অবশ্য একটা বড় কারণ আছে । তাহলো তার নেতৃত্বে আরও কয়েকটি গেরিলা দল মিলে আজ ভোর রাতে যশোর শহরের পূর্বের খাজুরা হাই স্কুল রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করে বেশ কিছু রাজাকারকে হত্যা করে সফলতা দেখিয়েছে। অপারেশনে মুক্তিযোদ্ধাদের এই সফলতার পেছনে মোঃ ইসহাক নামের একজন সামরিক প্রশিক্ষপ্রাপ্ত মুজাহিদ সদস্যের অবদান সবচেয়ে বেশি। মুক্তিযোদ্ধা দলের সদস্য না হয়েও সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং খাজুরা রাজাকার ক্যাম্পের পাশের লেবুতলার গ্রামে বাড়ি হওয়ায় ক্যাম্পটির সেন্টি পোস্ট ও অন্যান্য অবস্থান সম্বন্ধে তার স্পষ্ট ধারণা ছিল। সামরিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হওয়ায় যশোর অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে ইসহাক ইপিআর বাহিনীর সাথে প্রথম পর্যায়ের প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। সেই যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর প্রতিরোধ যোদ্ধারা ভারতে চলে গেলেও নতুন বিবাহিত স্ত্রী এবং পরিবারের অসুবিধার কথা ভেবে সে ভারতে যাওয়া থেকে বিরত ছিল। ভারত থেকে প্রশিক্ষণ শেষে মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশের ভেতরে প্রবেশ করার পর সে আর ঘরে বসে থাকতে পারেনি। মাজহারুল হক মন্টুর গেরিলা দলটি কাশিমপুর গ্রামে সেল্টার গ্রহণ করার পর থেকেই সে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করে মন্টু সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে। তারর যোগ্যতা এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করার প্রচণ্ড আগ্রহ দেখে মন্টু সাহেব তাকে নিজ দলে অন্তভূক্ত করে নেন।
কাশিমপুর গ্রামে সেল্টার গ্রহণ করার পর থেকেই খাজুরা হাই স্কুল রাজাকার ক্যাম্পের নানা অপকর্মের কথা মন্টু সাহেবের কানে আসছিল। মাত্র ১০/১২ দিনের মধ্যে ২টি বাড়ি লুট এবং বেশ কয়েকজন নারীর সম্ভ্রমহানীর সাথে তাদের নাম জড়িয়ে যাওয়ায় অন্যান্য গেরিলা কমান্ডারের সাথে আলোচনা করে মন্টু সাহেব খাজুরা রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আর একই এলাকায় বাড়ি, অবাধ যাতায়াতের সুযোগ এবং সামরিক বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়ায় ক্যাম্পটি সরেজমিনে রেকি করে একটা খসড়া আক্রমণ পরিকল্পনা প্রণয়ণের জন্য তিনি ইসহাককে দায়িত্ব প্রদান করেন। সেও সুযোগটি মনেপ্রাণে গ্রহণ করে। তারপর অবাধ যাতায়াতের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে একটা নিখুঁত আক্রমণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সে তা মন্টু সাহেবের নিকট জমা দেয়। সেই আক্রমণ পরিকল্পনা নিয়ে ৫ জন গেরিলা কমান্ডার আলোচনা করে সামান্য কিছু কাটছাট করে চুড়ান্ত করা হয়। তারপর মাযহারুল হক মন্টুর নেত্বত্বে ৫টা গেরিলা দলের ৫৫ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে আজ ভোর তারা রাতে খাজুরা রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করে শতভাগ সফলতা লাভ করে। শুধু যুদ্ধ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা নয়, ইসহাক অস্ত্র হাতে সরাসরি গুলিতে শত্রুর ২ জন সেন্টিকে হত্যা করে যুদ্ধ জয়ে অনেক ভূমিকা রেখেছে। তাইতো আজ সারাদিন ক্যাম্পে একটা আনন্দের আমেজ লেগে আছে। সাথে সাথে চলছে ইসহাক বন্দনা।
চলবে…
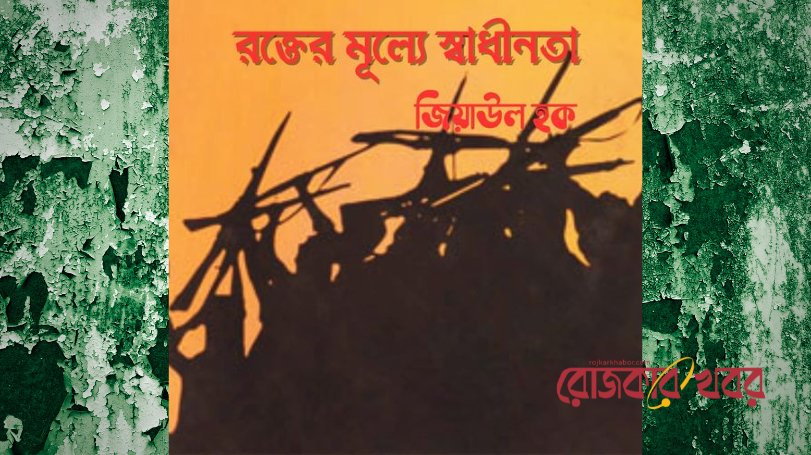
১৯৭১ সালের জুন মাসের শেষ দিক। বাংলাদেশে তখন চলছে পাকিস্তানি কসাই সেনাদের রক্তের হলিখেলা। ২৫শে মার্চের কাল রাত থেকে তারা সারা বাংলাদেশের নিরস্ত্র নিরীহ মানুষের উপর আক্রমণ চালিয়ে নির্বিচারে মানুষ হত্যার পাশাপাশি গ্রামের পর গ্রামে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, নারী ধর্ষণসহ নানা পৈশাচিক কর্মকাণ্ডে মেতে উঠেছে। অন্য দিকে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের সেই ঐতিহাসিক ঘোষণা– ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ দেওয়ার পর থেকেই দেশে শুরু হয়ে গিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি। ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার পর থেকেই সারা বাংলাদেশে শুরু হয়ে যায় প্রতিরোধ যুদ্ধ। এরই ধারাবাহিকতায় ১৭ই এপ্রিল প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ এবং তার অল্প কিছু দিনের মধ্যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু হয়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্যগাথা শুনে অবরুদ্ধ বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ যেমন উৎফুল্ল হয়ে উঠতো, তেমনি বাঙালি যুবকেরা মুুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে অনুপ্রেরণা খুঁজে পেত। যার ফলে দেশের ভেতর থেকে যুবক ছেলেরা দলে দলে ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে শুরু করে।
দিনে দিনে মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে পাকি সেনারাও নতুন ফন্দি আঁটে। নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য স্বাধীনতাবিরোধী জামাতে ইসলাম, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামসহ অন্যান্য স্বাধীনতা বিরোধী দলের সহযোগিতায় তারা রাজাকার, আল বদর, আল শামস বাহিনী গঠন-কাজে হাত দেয়। জুন মাসের প্রথম দিকে তাদের এই বাহিনী গঠন-প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই মাসের মাঝের দিকে জামাত নেতা লেবুতলা গ্রামের ইব্রাহিম ডাক্তারের নেতৃত্বে (হাতুরে ডাক্তার) যশোর শহর থেকে ২০ মাইল পূর্বে খাজুরা উচ্চ বিদ্যালয়ে একটা রাজাকার ক্যাম্প স্থাপন করার পর থেকেই তারা গ্রামের সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার, নির্যাতন, বাড়িঘর লুটপাট এবং নারী ধর্ষণের মতো গর্হিত কাজ শুরু করে দেয়। শুধু তাই না মাত্র ১০/১২ দিনের মধ্যেই লেবুতলা গ্রামের নিমাই কাপালি, গৌর মাষ্টারের বাড়িতে লুটপাট ও খাজুরার আলিয়র রহমানের স্ত্রী ও ২ বোনকে ধরে নিয়ে গিয়ে সম্ভ্রমহানী করার পর তারা এলাকায় মূর্তিমান আতঙ্কে পরিণত হয়ে গেছে। এখন গাঁয়ের মানুষদের জলে কুমির আর ডাঙায় বাঘের মতো অবস্থা। প্রতি রাতেই যেমন পাকিস্তানি কসাই সেনারা বিভিন্ন এলাকায় আক্রমণ চালাচ্ছে, তেমনি দিনের বেলায় রাজাকার ও আল বদরেরা গ্রামে গ্রামে হামলা চালিয়ে লুটপাট ও নানা অসামাজিক কাজে মেতে উঠছে। শত্রুদের এই দ্বিমুখী আক্রমণে আজ বাংলাদেশের প্রতিটা এলাকায় নরকের যন্ত্রণা নেমে এসেছে। তাদের জীবন ও জীবিকা এলোমেলো হয়ে গেছে।
খান সেনাদের আক্রমণের আগাম খবর জানার জন্য এখন মানুষ তাদের রাতের ঘুমকে হারাম করে গাঁয়ে গাঁয়ে সারা রাত পাহারা বসিয়েছে। নির্ঘুম রাত কাটানোর পর দিনের বেলায় যে একটু শান্তিতে ঘুমাবে তারও কোন উপায় নেই। কারণ কখন যে রাজাকার আল বদরেরা হামলা করে বাড়ি ঘরে লুটপাট কিংবা যুবতি নারীদের অপহরণ করে নিয়ে যায় সেই চিন্তায় তাদের উৎকন্ঠিত থাকতে হয়। দিনের আলোয় তবুও মনে একটু বল পাওয়া যায়। কিন্তু রাতের আঁধার ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে মানুষের জীবনও যেন ঘোর অন্ধকারে ছেয়ে যায়। তখন তাদের মাথায় একটাই চিন্তা ঘুরপাক খায়– পরিবারের সবার জীবন রক্ষা করতে পারবো তো? বাড়ির যুবতি মা, বোন, কন্যার সম্ভ্রম রক্ষা করা যাবে তো? রাত যত গভীর হতে থাকে মানুষের মনের আতঙ্কও ততো বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরই মধ্যে এলাকায় জোর গুজব ছড়িয়ে পড়েছে যে ভারত থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা দেশের ভেতরে প্রবেশ করেছে। কেউ তাদের চোখে দেখেনি। তবুও এই খবর শুনে সাধারণ মানুষ আশায় বুক বাঁধতে শুরু করেছে। এবার নিশ্চয়ই মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে পাকিস্তানি সেনা তথা রাজাকার আলবদর বাহিনী পরাজিত হবে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। কিন্তু সেই স্বাধীনতার জন্য আর কত দিন আর কত রাত তাদের এমন দুঃসহ যাতনা ভোগ করতে হবে?
আজ ৩০শে জুন। জুন মাসের শেষ দিন। মানুষ জন সারা রাত গাঁ পাহারা দিয়ে ঘরে ফেরা শুরু করেছে। মসজিদে মসজিদে মুয়াজ্জিনের আজানের ধ্বনি ভেসে আসছে। ঠিক এমন সময় খাজুরিয়া রাজাকার ক্যাম্পের উপর যেন গুলির বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হয়ে গেছে। এলএমজি, এসএলআর, ৩০৩ রাইফেলের গুলি ও গ্রেনেড বিস্ফোরণের শব্দের পাশাপাশি মুর্হুমুহু ভেসে আসছে জয় বাংলা স্লোগান। তখন এলাকার মানুষের মনের সব সংশয় দূর হয়ে যায়। তারা নিশ্চিত হয়ে যায়, নরাধম রাজাকাদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে মুক্তিযোদ্ধারাই খাজুরা রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করেছে। সারা ক্যাম্প এলাকায় যেন ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। সেই ভূমিকম্প যেন থামতেই চায় না। প্রায় ঘন্টা খানেক প্রবল গুলাগুলি চলার পর আস্তে আস্তে তা স্তিমিত হয়ে আসে। এরই মধ্যে পূর্ব আকাশে নতুন দিনের আশার সূর্য উদিত হতে দেখা যায়। দিনের আলোয় আশে পাশের বাড়িঘরের লোকজন ক্যাম্পের সামনে এসে দেখতে পায় ৫ জন রাজাকার মরে পড়ে আছে। বাকিরা জীবন বাঁচাতে ক্যাম্পের পিছনের ডোবায় আশ্রয় নিয়েছিল। মুক্তিবাহিনী চলে যাওয়ার পর আস্তে আস্তে তারা ক্যাম্পে ফিরে আসছে। নরাধমদের এমন উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে দেখে গাঁয়ের লোকজন মনে মনে ভীষণ খুশি হলেও তারা মুখে তা প্রকাশ করতে পারে না। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সেদিনের রাতের খবরে যশোর জেলার খাজুরা রাজাকার ক্যাম্পের উপর মুক্তিযোদ্ধাদের সফল অপারেশন পরিচালনার খবর ফলাও করে প্রচার করার সাথে সাথে তা ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বময়। এই খবর পেয়ে অবরুদ্ধ বাংলাদেশের প্রতিটা মুক্তিপাগল বাঙালির মনে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সেদিনের চরমপত্র অনুষ্ঠানে শোনা গেল– বিচ্ছুদের গাবুড় মাইরের চোটে যশোরের খাজুরায় ৫ জন রাজাকার অক্কা পেয়েছে। বাকিরা জীবন বাঁচাতে ক্যাম্পের পেছনের ডোবার ভেতরে হাবুডুবু খেয়েছে।